নদীমাতৃক বাংলাদেশের উদ্ভিজ কিছু হস্তশিল্পে
বাংলাদেশের উদ্ভিজ হস্তশিল্প
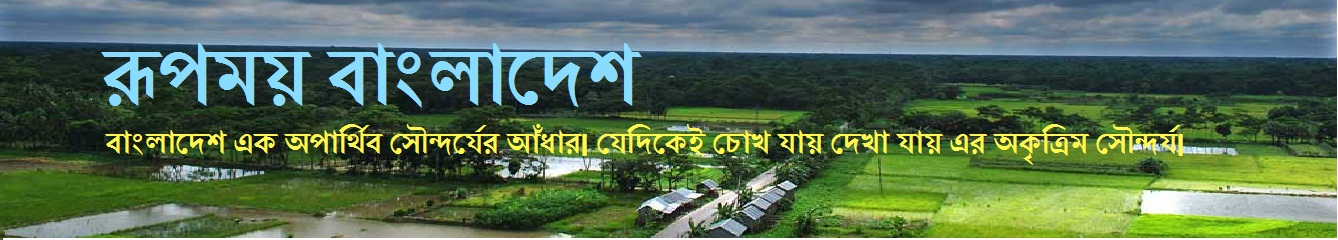
নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে গাছপালা, বাঁশ, বেতসহ সবুজ শ্যামলীময় পরিবেশ সৃষ্টিতে হরেক রকম উদ্ভিদ জন্মে। অনুকূল পরিবেশ হওয়ায় এসব গাছগাছালি, ঝোঁপঝাড় এমনিতেই জন্মে থাকে, কোনোরকম চাষাবাদ করতে হয় না। জমি পতিত থাকলেই সেখানে উদ্ভিদ জন্মে গড়ে ওঠে বনজ পরিবেশ।
সহজেই পাওয়া যায় বলে উদ্ভিদ হয়ে ওঠে শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম। ব্যবহারিক সামগ্রী তো বটেই, শোভাবর্ধনমূলক শিল্পসামগ্রীও সৃষ্টা করা হতে থাকে উদ্ভিদ দিয়ে। কাষ্ঠল বৃক্ষ, নলখাগড়া, বাঁশ, বেত ইত্যাদি হয়ে ওঠে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের অন্যতম উপকরণ। এ অংশে উদ্ভিজ কিছু হস্তশিল্পের বিবরণ দেওয়া হলো।
কাঠের শিল্পকর্ম বা দারুশিল্প

মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে কাঠকে তার হাতিয়ার, গৃহ এবং তৈজসপত্র নির্মাণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছে। কাঠ শিল্পকর্মেরও উপাদান। শিল্পকর্ম হিসেবে কাঠ বা দারু ব্যবহার হয়েছে ধর্মীয় কেন্দ্রকে আশ্রয় করে। এক সময় ধর্মকেন্দ্র অর্থাৎ মন্দির, মসজিদ ও গির্জা ছিল মানুষের সকল কর্মের প্রেরণার উৎস। ক্রমে দারুশিল্প স¤্রাট, রাজা বাদশাহদের প্রাসাদে পদার্পণ করে। বর্তমানে দারুশিল্প পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে সমাদৃত। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পীদের কাছে পাথর বা ধাতু অপেক্ষা কাঠ ছিল সহজলভ্য ও নমনীয়। কাঠ কেবল সহজলভ্যই ছিল না, কাঠ এ অঞ্চলের মানুষের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, শৌখিন জিনিস ইত্যাদির প্রয়োজন একই সঙ্গে মিটিয়েছে। স্থায়িত্বের দিক থেকে কাঠ পাথর বা ধাতুর চেয়ে পচনশীল, ক্ষয়িষ্ণু ও কীটদুষ্ট হয়ে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।এছাড়া আবহাওয়াগত কারণেও এ অঞ্চলে কাঠের জিনিস সহজে বিনষ্ট হয়। ফলে কাঠের সুপ্রাচীন নিদর্শন আমরা খুবই কমই পাই। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় কাঠ শুধু ব্যবহৃত হতো না, সে সময়ে এর গুণগত মান নিয়েও চিন্তা করা হতো। রামায়ণ মহাভারতেও দারুশিল্পীদের অলঙ্কৃত গৃহদ্বার, রথ, সিংহাসন ইত্যাদি তৈরির উল্লেখ আছে।
মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাঠের প্রাসাদের এবং পাটলিপুত্রের দারুকর্মের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাঠের তৈরি বিশাল রাজপ্রাসাদটি ছিল দারুভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।
প্রাচীন বাংলায় নৌশিল্প ছিল দারুশিল্পের একটি অঙ্গ। রায় উল্লেখ করেছেন , নদীগামী ছোটবড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসা প্রাচীন বাংলার নিশ্চয় ছিল। শিল্পশাস্ত্র বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কাঠের আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সম্পর্কে যে আলোকপাত করা হয়েছে তা থেকেও দারুশিল্পের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে নৌকা, সিংহাসন, খাট-পালঙ্ক ইত্যাদি তৈরিতে বিভিন্ন কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে নৌকা তৈরির জন্য চার প্রকার কাঠের উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠের সমন্বয়ে তৈরি নৌকা সুখকর ও মঙ্গলদায়ক ছিল না।
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলার শিল্পে, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে প্রভৃতি উন্নতি সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মমত বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই কেবল প্রভাব ফেলেনি, সাধারণ মানুষের কাছে এর জনপ্রিয়তার কারণে সে সময়ের শিল্পকর্মে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী চিত্রিত ও ক্ষোদিত হয়েছে দারুশিল্পে। শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনের ও বাদ্যযন্ত্রের সাথে নৃত্যের দৃশ্য উনিশ শতকের কৃষ্ণভক্তের গৃহের কাঠের বেড়ায় ক্ষোদিত হয়েছে। এছাড়াও উনিশ শতকের কাঠের শিল্পকর্মে কৃষ্ণের জীবনকাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন দৃশ্য খোদিত হয়েছে। এর মধ্যে কৃষ্ণের বাল্যজীবন, কৃষ্ণের গোচারণ দৃশ্য, কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ অন্যতম। এসব দৃশ্য যে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলায় জনপ্রিয় ছিল তা কাঠের শিল্পসামগ্রী থেকে অনুমিত হয়। এ সকল শিল্পকর্ম সৃষ্টির পিছনে গৃহস্বামী ও সূত্রধর উভয়েরই অবদান ছিল। এ সময়ের অধিকাংশ সূত্রধর ছিল বৈষ্ণব। তাই কাঠের শিল্পকর্মে এ ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়।

মুঘল আমলে বাংলার সাথে ভারতের অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ দৃঢ় হলে শিল্পকর্মে ও স্থাপত্যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। সপ্তদশ শতকে অর্থাৎ বাংলার বারো ভূঁইয়াদের আমলে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ব্রাক্ষণ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তান্ত্রিকবাদ ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। ফলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি ইংরেজ রাজত্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সমাজে নতুন যুগের সূচনা করে। শিল্পস্থাপত্যে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে মাটি, পাথর ও কাঠের শিল্পকর্মে বিদেশী প্রভাব দেখা যায়।
ভাস্কর্যে, মন্দিরে ও দরজায় দারুশিল্পের অলঙ্করণ যেমন আর্থ-সামাজিক কারণে ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি গৃহ ও আসবাবের ক্ষেত্রেও সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক ছিল চরম উৎকর্ষের যুগ। প্রাচীন ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থা বর্তমানের চাইতে উন্নত থাকায় সে সময়ের আসবাব, দেবমূর্তিসহ সকল কিছুতেই ছিল চিকচিক্যের ছাপ। দারুনির্মিত অনেক কিছুতেই তখন খোদিত হয়েছে মূল্যবান পাথর, সোনা রূপার পাত ও গজদন্ত, এবং এসব নির্মিত হয়েছিল শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী। রাজকীয় আসবাব ছিল সাধারণের চাইতে উন্নত এবং চাকচিক্যপূর্ণ। সূত্রধরেরা শাস্ত্রীয় নির্দেশ মতে এবং নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী শিল্পকর্ম সৃষ্টি করত। পরবর্তীকালে আসবাব, গৃহদ্বার ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে না চলে গৃহকর্তা বা সূত্রধরদের নিজস্ব শৈলীতে দারুশিল্পকর্ম তৈরি হতে থাকে।
ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামল থেকে ব্রিটিশ রাজত্বকাল পর্যন্ত পালঙ্কের অলঙ্করণশৈলীতে পরী, বিদ্যাধর ও মিথুন দৃশ্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ ধরনের পরী সম্বলিত উনিশ শতকের কয়েকটি পালঙ্ক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলায় দারুশিল্পের যে ঐতিহ্য দারুশিল্পীরা ধরে রেখেছিল সে ধারা বাংলাদেশেও দারুশিল্পে নানা শ্রেণীর আসবাব, স্থাপত্যাংশ, দেবদেবীর, ভাস্কর্য, বেড়া, সিন্দুক, পালঙ্ক, পালকি, চেয়ার, টেবিল, নানা ধরনের প্যানেল, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, ঢেঁকি, কাইয়াল, সিড়ির রেলিং, দেওয়াল তাক, দরজা ও স্তম্ভ কাজেও সূক্ষ্মতায় বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
বাংলাদেশের দারুশিল্পের নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর নিজস্বতা। এখানকার দারুশিল্পীরা কাঠে নকশার খোদাই কাজ করতে গিয়ে দুই ধরনের শৈলী প্রয়োগ করেছে। একটি ধ্রুপদী শৈলী অপরটি লোকায়ত শৈলী। ধ্রুপদী শৈলীর ক্ষেত্রে দারুশিল্পীরা খোদাই কাজের সর্বত্র ছন্দ ও ভারসাম্যতা মেনে চলেছে এবং লোকায়ত শৈলীতে দারুশিল্পী তার নিজস্ব চিন্তা চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছে সর্বত্র। সে অনুসারে প্রাচীন হতে অদ্যাবধি বাংলার দারুশিল্পের যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার মূলে ছিল নকশা বা অলঙ্কণের বৈচিত্র। মৌর্যযুগে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাঠের তৈরি রাজপ্রাসাদ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রাসাদের বাইরের ও ভিতরের অলঙ্কৃত আসবাবে, স্তম্ভে ছিল সূক্ষ্ম কারুকাজমন্ডিত নকশার সমাহার। এসব নকশা তৈরিতে সূত্রধরদের যেমন অবদান ছিল তেমনি ছিল রাজা বা বিত্তবান সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা।
ষোড়শ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার দারুশিল্পে নিজস্ব নকশার পাশাপাশি ইউরোপীয় নকশারও প্রভাব পড়েছিল। বাংলার সাথে বিদেশী বণিকদের ব্যবসায়িক লেনদের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে এবং বাংলায় বিদেশী নকশার যেমন সমাবেচশ ঘটেছে তেমনি এদেশীয় নকশার প্রভাও ইউরোপীয় দেশগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। এদেশীয় নব্য জমিদার শ্রেণী, চাকরিপ্রাপ্ত কর্মচারী ও বিত্তবানদের দেশীয় নকশার চেয়ে ইউরোপীয় নকশার প্রতি অধিক আকর্ষণ ছিল। ফলে কোন ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী নকশার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আবার কোনো কোনো নকশায় সম্পূর্ণ বিদেশী ছাপ পড়েছে। মুগল আমলেও আসবাব, স্থাপত্যকলায় পড়েছে বিদেশী প্রভাব। এ সময় থেকে বিশেষ করে ইউরোপীয় প্রভাবে তৈরি হয়েছে দরবারগৃহের ও আন্দরমহলের আসবাবপত্র। অষ্টাদশ থেকে উনিশ শতকের বিদেশী নকশা দারুশিল্পের বিভিন্ন বস্তুর গঠনশৈলীতে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল।
বিদেশী প্রভাবযুক্ত নকশার মধ্যে স্তম্ভ, খিলান, বোরাক, পরস্পর আবদ্ধ নকশা, জ্যামিতিক নকশা, ফুলদানিতে উত্থিত পুষ্পরাজি অন্যতম। এ ধরনের নকশা কাঠের বেড়া, সিন্দুক, দরজা ও চৈত্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে নির্মিত দালান কোঠায় প্রায় একই ধরনের খিলান, স্তম্ভ, অ্যাকান্থাস জাতীয় পত্রগুচ্ছ অলঙ্করণে দেখা যায়। এ ছাড়া কলকা, মোচড়াফুল, বৃক্ষ, প্যাঁচানো সর্প, জালিকাজ, অ্যাকান্থাস, বালবাস, প্যাটেরা, থাবা পায়া, মশারির ছত্রী নকশা, ক্যান্ডিলাব্রা নকশা, প্রতিস্থাপিত নকশা, পাখি সম্বলিত পত্রগুচ্ছ, শতদল পদ্ম নকশা, আঙ্গুর লতাপাতা নকশা, বাংলাদেশের দারুশিল্পে ব্যাপকভাবে ক্ষোদিত হয়েছে। এসব নকশার মধ্যে বর্তমানে জনপ্রিয় হয়েছে ফুল, লতাপাতা নকশা। পশুপাখি বা কোন জীবজন্তুর নকশা বর্তমানের দারুশিল্পে দেখা যায় না।
একবিংশ শতকে বাংলাদেশে দারুশিল্পের আসবাবপত্র নতুন আঙ্গিকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ সময়ের আসবাবের খোদাই কাজে ফুল লতাপাতার নকশা ও খিলান ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে দারুশিল্পে খোদাইকাজ দুভাবে হয়ে থাকে হাতে ও মেশিনে। মেশিনের খোদাইকাজ সূক্ষ্ম কারুকাজের কাঠের শিল্পকর্ম তৈরি করতে খরচ বেশি পড়ায় কেউ এ ধরনের আসবাব তৈরী করাতে আগ্রহী হয় না, ফলে দক্ষ দারুশিল্পীরা নিজস্ব ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এবং তাদের সন্তানদের এ পেশায় আনতে অনিহা প্রকাশ করছে। আর্থসামাজিক কারণে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দারুশিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা কোন কৌলিক বৃত্তিকেই টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না বলে দারুশিল্পীরা ক্রমান্বয়ে অন্য পেশায় নিজদেরকে নিয়োজিত করছে। আমাদের উচিত এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে টিকিয়ে রাখা। এদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারলে আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী দারুশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হব।
বেত শিল্প
নদীমাতৃক দেশ বলেই বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে গাছ জন্মে। সাধারণত পতিত জমি থাকলেই গাছপালার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর তাই বিভিন্ন ধরনের গাছ বাংলাদেশের মানুষের শিল্প তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীন হস্তশিল্পের একটি হচ্ছে বেতশিল্প। অতীতে বেত দিয়ে যারা জিনিস তৈরি করতেন তারা বেশিরভাগই ছিলেন তপশিলভুক্ত জাতি অথবা আদিবাসী সমপ্রদায়ের মানুষ। বৃহত্তর সিলেট জেলার অধিকাংশ এলাকাতে অত্যন্ত ভালো জাতের বেত জন্মে। তাই এসব এলাকায় বেতশিল্পের প্রসারও বেশি। বেতের চেয়ার, বাসন-আসন চৌপাই, তেপাই, মোড়া, দাঁড়িপাল্লা, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করে নারী-পুরুষ উভয়েই।
বেতগাছ বনজঙ্গলে অথবা পাহাড়ি ঢালে জন্মে। তীক্ষ্ম কাঁটাযুক্ত একরকমের শক্ত লতার নাম বেত। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ও কৃষিজমি বৃদ্ধির কারণে জঙ্গল কমে যাওয়ায় বেতের উৎপাদন কমে গেছে।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও ও সুঁইামগঞ্জ এলাকার কারিগররা প্রচুর পরিমাণের বেতের শিল্প তৈরি করেন। বেতের জিনিস তৈরি করা অত্যন্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যের কাজ। একজন দক্ষ কারিগর সাত-আট ঘন্টা পরিশ্রম করে মাত্র দুটি বেতের মোড়া তৈরি করতে পারেন। অনেক বেতের সামগ্রী তৈরি করতে বাঁশ ও দড়ির প্রয়োজন হয়। যেমন বেত ছাড়া যেমন মোড়া হয় না, তেমনি দড়ি ও বাঁশ ছাড়া মোড়া তৈরি করা যায় না। বাংলাদেশের জেলখানার কয়েদীরা তাদের অবসরে নানা বেতের সামগ্রী তৈরি করেন। এসব সামগ্রী বিক্রির জন্য জেলখানার নিজস্ব শোরুমও রয়েছে।
বেত দিয়ে নানান ব্যবহার্য আসবাবপত্র যেমন তৈরি হয়, তেমনি শৌখিন জিনিসও তৈরি হয়। বেত একই সাথে দেশজ ও অভিজাত বলে অনেকেই বেতের আসবাবপত্র দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করে। তবে বেতের জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক বেশি হওয়ায় তা অনেকেরই নাগালের বাইরে।
বাঁশ শিল্প

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে জঙ্গল, গাছপালা, বাঁশ ও বেতসহ প্রচুর পরিমাণে সবুজ শ্যামলীময় পরিবেশ সৃষ্টিতে হরেক রকমের উদ্ভিদ জন্মে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়, উঁচু-নিচু ও সমতল সবখানেই বাঁশ গজায়। বাঁশ এক ধরনের খাগড়া জাতীয় গাছ, উচ্চতায় অনেক বেশি লম্বা।
বাঁশ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা থাকায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে বাঁশ ব্যবহার করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবকূলে বাঁশ ব্যবহৃত। যেমন: ছটির ঘর শিশু জন্মালে তার নাড়ি কাটা হয় কাঁচা বাঁশের ছিচকা দিয়ে এবং মৃতের কবর দেওয়া হয় বাঁশ দিয়ে।
বাঁশ বন-জঙ্গলে বিনা পারিশ্রমিকে ও পরিচর্যায় উৎপাদিত হয়। এক ধরনের লম্বা চোঙ্গা ও গিটা নিয়ে ৩৫/৪০ ফুট দীর্ঘ হয়ে থাকে। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার অপরিহাযর্। বাংলাদেশের সর্বত্রই বাঁশ জন্মে। বাঁশ নানা জাতের হয়ে থাকে যেমন, মুলি বাঁশ, বাকলা বাঁশ, জাতি বাঁশ, বেরু বাঁশ, ওলতা বাঁশ ও জংলি বাঁশ। এর মধ্যে একমাত্র জংলি বাঁশ, যেটি জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হয়, অন্য কাজে তেমন একটা ব্যবহার করা যায় না।
বাঁশ থেকে নানা গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরি করেন হিন্দু ও আদিবাসী সমপ্রদায়ের গরিব শ্রেণির মানুষ। তাদের মৌসুমি অবসরে কুলো, ঢাকী, ধুচুনি, ঝোড়া, টুকরি, চুপড়ি, মাছ ধরার যন্ত্র ইত্যাদি ঘরে বসে তৈরি করে স্থানীয় হাটবাজারে বিক্রয় করে। অনেকে গরু-মহিষের গাড়ির ছই-দরমা ইত্যাদিও তৈরি করে।
ছই বানাতে বাঁশ কারিগরদের প্রচুর মেহনত ও শ্রম ব্যয় করে তেমন মূল্য পান না। ওলনা বাঁশুনী বাঁশকে খুব সরু করে ফালি করে তা থেকেই ছই বা চাঁচ এবং ঘুনি, মুগরী, পাং, হালুক নামের নানা মাছ ধরার যন্ত্র বানায়। হাল আমলে শিল্পীরা বাঁশ দিয়ে কলমদানি ছাইদানি, বিয়ার মগ ও দেওয়াল চিত্রের ফ্রেম ইত্যাদি প্রস্তত করে। বর্তমানে বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র শিক্ষিত সমাজের ঘরে ব্যবহার করতে দেখা যায়।
বাঁশ-বেত দিয়ে নানা রকম মাছ ধরার যন্ত্র তৈরি করা হয়। যেমন হোচ (হোচা), কোচ, কোলে, টেটা, একনালা, বানা, নানা প্রকারের বাইস (আটস) আওড়া, খুদল, খুলি, ঠসি, বগি এবং বাঁশ দিয়ে পোলো, দোয়ার, ভোমরু, ছানাই (চট্টগ্রামের চাকমাদের), ঘুনি বা ঘুনসি, বাইচা, ছাওড়া, তুবু, ঝিমরি ইত্যাদি। সাঁওতালদের বাঁশ বেতের খরপোষ অভিনব অপরূপ হস্তশিল্প।
মাদুর ও হোগলা শিল্প
বাঁশ-বেত দিয়ে নানা রকম মাছ ধরার যন্ত্র তৈরি করা হয়। যেমন হোচ (হোচা), কোচ, কোলে, টেটা, একনালা, বানা, নানা প্রকারের বাইস (আটস) আওড়া, খুদল, খুলি, ঠসি, বগি এবং বাঁশ দিয়ে পোলো, দোয়ার, ভোমরু, ছানাই (চট্টগ্রামের চাকমাদের), ঘুনি বা ঘুনসি, বাইচা, ছাওড়া, তুবু, ঝিমরি ইত্যাদি। সাঁওতালদের বাঁশ বেতের খরপোষ অভিনব অপরূপ হস্তশিল্প।
মাদুর ও হোগলা শিল্প

বাংলার গ্রাম অঞ্চলের মানুষ গরমের দিনে মাদুর ব্যবহার করে। তৃণ নির্মিত এক ধরনের পাটি। মাদুর শিল্প এক ধরনের পাটি তৈরির কুটির শিল্প। আমাদের গ্রাম বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে মাদুর ব্যবহার হয়ে আসছে। নিম্ন আয়ভূক্ত মানুষ মাদুর লতা ছিঁড়ে রৌদ্রে শুকিয়ে মাদুর বানায়, এজন্য কোনো গোত্র বা ধর্মের মানুষ নির্ধারণ করা নেই।
মাদুর লতা বৃষ্টিবহুল এলাকায় না জল অথবা না শুকনা এমন স্থানে মাদুর লতার গাছ জন্মে। এই লতাগাছের কোনো ডালপালা হয় না, ভেতরটা ফাঁকা থাকে। একটু নাড়া দিলে অথবা বাতাসের ঢালে ঢেলে পড়তে পারে। গাছটি সংবেদনশীল। লতাগাছটি কাঁচা অবস্থায় কেটে নিয়ে রৌদ্রে শুকানোর আগে ছুড়ি বা চাকু দিয়ে বুক ছেঁচে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে মাদুর তৈরি করা যায়।
মাদুর তৈরির তাঁত চারটি বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি করা হয়। দুই ফুট থেকে আড়াই ফুট খাড়াই খুঁটি, তিন ধারে বাঁশের ঘেরা পাঁচ ফুট লম্বা। দেড় ইঞ্চি মোটা ব্যাস। এছাড়া লাগে কাঠের হাতা আর যাঁতা। হাতার মাপ আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি এবং চওড়ায় দেড় ইঞ্চি মোটা। মাদুর বসে বসে তৈরি করতে হয়। মাদুর কারিগরেরা চার শ্রেণীর তৈরি করে যেমন- একহারা, দোহারা, কেলে এবং মেলে।
মাদুর লতাগাছ যে পাটি তৈরি করা হয় তাকে মাদুর পাটি, শীতল পাটি ঘাস যে পাটি হয় তা মোথরা পাটি, হোগলা গাছের লতা থেকে যে পাটি তা হোগলা পাটি এবং মোর্তা গাছের থেকে যে পাটি তা মোর্তা পাটি বা শীতল পাটি বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা এবং কিশোরগঞ্জের হাওর-বাঁওড় বিল-ঝিলের ধারে মাদুর লতার গাছ জন্মে কোনো রকম পরিচর্যা ও যতœ ছাড়াই। মাদুর পাটি নির্মাতারা কাঁচি অথবা দা দিয়ে কেটে নেয়। নির্দিষ্ট জাতের-বর্ণের কারিগর না থাকায় যে কেউ তাদের প্রয়োজনে মাদুর পাটি তৈরি করে। এই মাদুরে তেমন কোনো কারুকাজ থাকেনা, তাই যে কেউ অনায়াসে তৈরি করতে পারে।
আধুনিক যুগে প্লাস্টিকের পাটি ব্যবহার ও ধৌত করা সহজ, মূল্যও খুব বেশি নয়, বহুদিন টেকসই হয়, ফলে মানুষ অধিকতর সুবিধার কারণে দেশীয় মাদুর পাটি ব্যবহার করতে চায় না। যার কারণে দেশীয় মাদুর পাটি বাজারে বিক্রয় হয় না। তাদের মাদুর পাটি ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায় কারিগররা বিকল্প পেশা গ্রহণ করেছে, পরিণামে মাদুর পার্টি বুনন ও ব্যবহারে আজ বিলুপ্তির পথে।
শীতল পাটি
বাংলাদেশের লোকশিল্পের মধ্যে প্রায় বিলুপ্ত একটি শিল্প হচ্ছে শীতলপাটি। এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে শীতলপাটি ব্যবহার হলেও প্লাস্টিকের পাটি বা কার্পেট সহজলভ্য হওয়ায় শীতলপাটি এখন হুমকির মুখে। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ পাটির কদর রয়েছে। পাটিপাতা দিয়ে তৈরি এই পাটিতে শুয়ে গরমের দিন আরাম পাওয়া যায় বলে এ পাটিকে শীতলপাটি বলা হয়।
বেতের সরু খিল মূর্তা বেতা বা মোত্রাবেত অথবা নলখাগড়া দিয়ে শীতলপাটি তৈরি করা হয়। বরিশাল, পটুয়াখালি, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি, ফেনী, চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে পাটিপাতার গাছ জন্মে। সিলেটের বালাগঞ্জের পাটি এখনো শীর্ষে রয়েছে।
শীতলপাটিতে গাছপালা, লতাপাতা, পশুপাখি, জ্যামিতিক নকশা, মসজিদ, মিনার, পালকি, নৌকা, হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি নানা নকশা পাটিপাতার বুননের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। অনেক সময় পাটিপাতা রঙ করেও রঙিন অনেক নকশা চিত্রিত করা হয়। এ কারণে চিত্রিত বা নকশাকৃত এই পাটিকে নকশীপাটিও বলা হয়।
বাংলাদেশের জলাভূমির অংশগুলোতে, পুকুর পাড়ে, খাল বা ডোবা কিংবা জলাশয়ে একপত্রী এক কান্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ জন্মে যার নাম। এই গাছটিই শীতলপাটি বা নকশীপাটির মূল উপাদান। পুরুষরা বেত কেটে ফালি করে এবং মেয়েরা বেতি ছাড়ায়। ভাতের মাড় ও পানি মিশিয়ে বেতি জ্বাল দেওয়া হয় রঙ সাদাটে করার জন্য। নারী-পুরুষ তো বটেই শিশুরাও পাটি বোনে। নকশীপাটিতে ব্যবহৃত রঙ যেন আরো ভালো ভাবে বোঝা যায় তার জন্য বেতিকে আরেক উপায়ে আরো সাদা করে তোলা হয়। ভাতের মাড়ের সাথে ভেষজ টক মিশিয়ে বেত সেদ্ধ করলে এর রঙ আরো সাদা হয় এবং বেতির মসৃণতা বৃদ্ধি পায়।
নকশা আঁকা শীতলপাটি তৈরি করতে খুব বেশি সময় না লাগলেও বাজারে যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকায় এর পরিধি ছোট হয়ে যাচ্ছে। ফলে নকশীপাটি বা শীতলপাটির উৎপাদনও কমে যাচ্ছে।
শীতলপাটি বিলুপ্তির মুখে হলেও এর কিছু ব্যবহার এখনো দেখা যায়। বিশেষ করে বিয়েতে নকশীপাটি দেওয়ার প্রথা বেশ কিছু জায়গায় প্রচলিত আছে। গরমের সময় গ্রামাঞ্চলেও এর ব্যবহার বেড়ে যায়।
শীতলপাটির কিছু শহুরে ব্যবহারও রয়েছে। যারা দেশীয় ঐতিহ্য দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করেন, তারা ঘরে কার্পেটের পরিবর্তে শীতলপাটি ব্যবহার করেন। নকশীপাটি বাঁধিয়ে দেওয়ালসজ্জার কাজেও ব্যবহার করেন। শীতলপাটির আদলে বোনা টেবিলম্যাটও পাওয়া যায় আজকাল। নকশীবা শীতলপাটি ঘরের সিলিং বা চালের নিচে লাগিয়ে ঘরের উপরের অংশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। নামায আদায়ের জন্য শীতলপাটির ব্যবহার রয়েছে।
মোটকথা, মানুষের ব্যবহারে ওপর নির্ভর করবে একটি শিল্পের পুনরুদ্ধার। তাই শীতলপাটির বর্ণিল ব্যবহারে যেমন গৃহ পাবে দেশজ ছোঁয়া, তেমনি পাটিশিল্প উদ্ধারে রাখা যাবে অবদান।

মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন